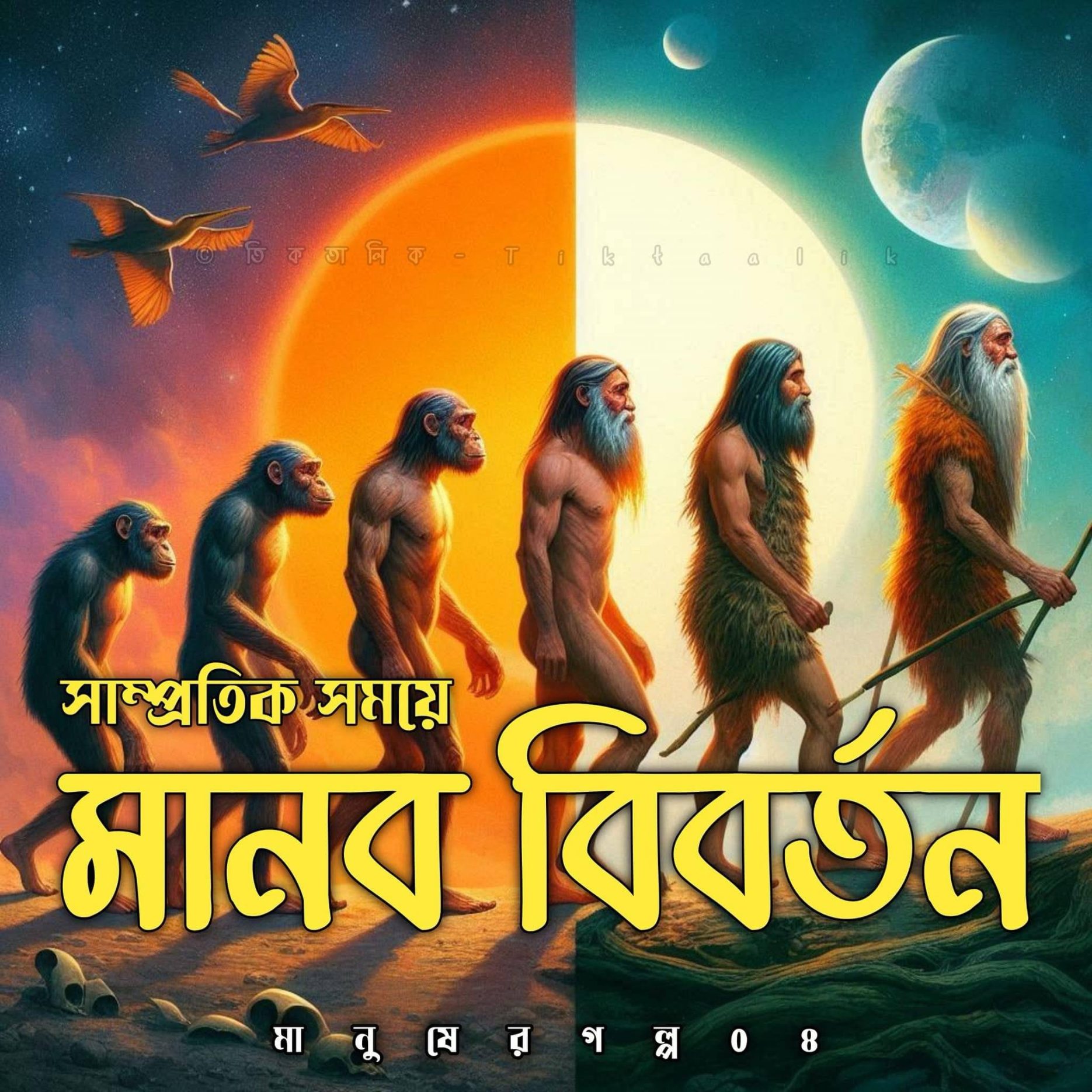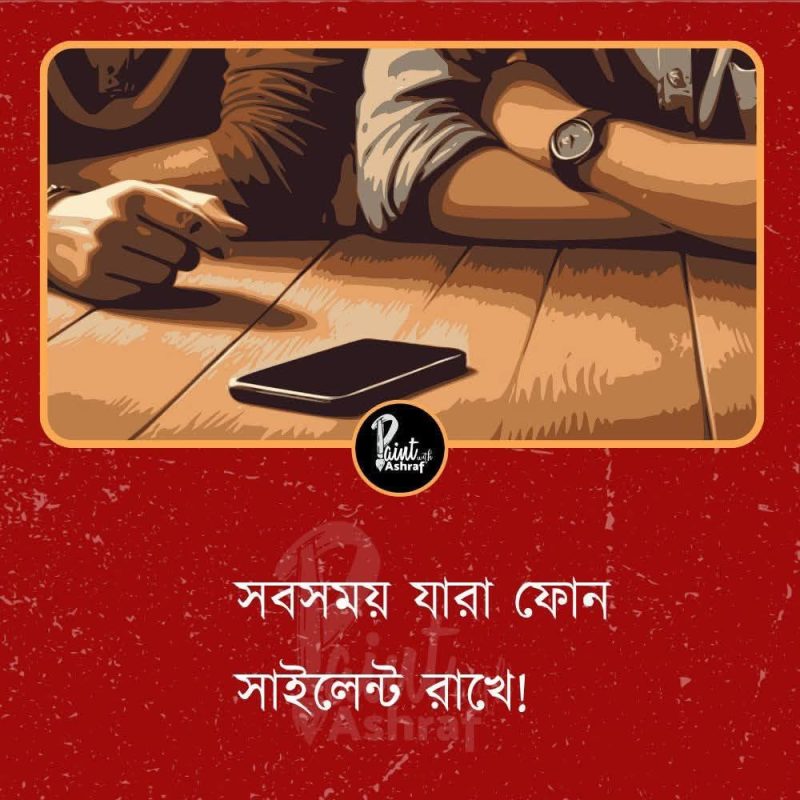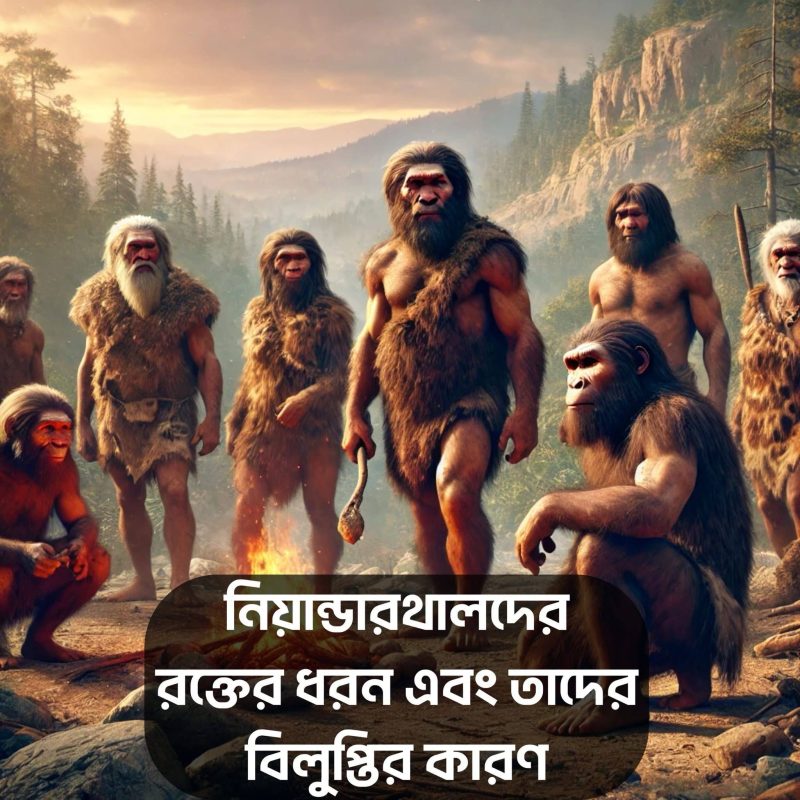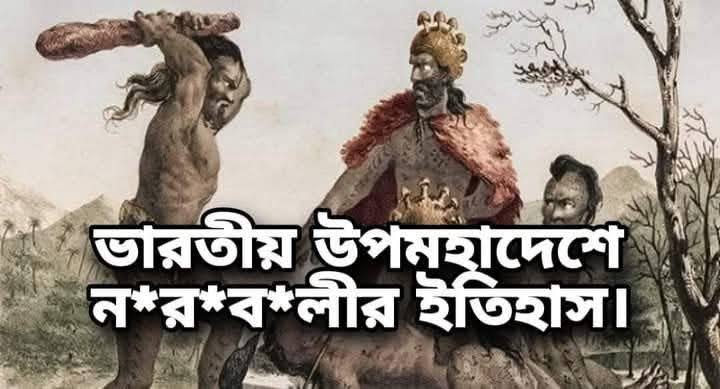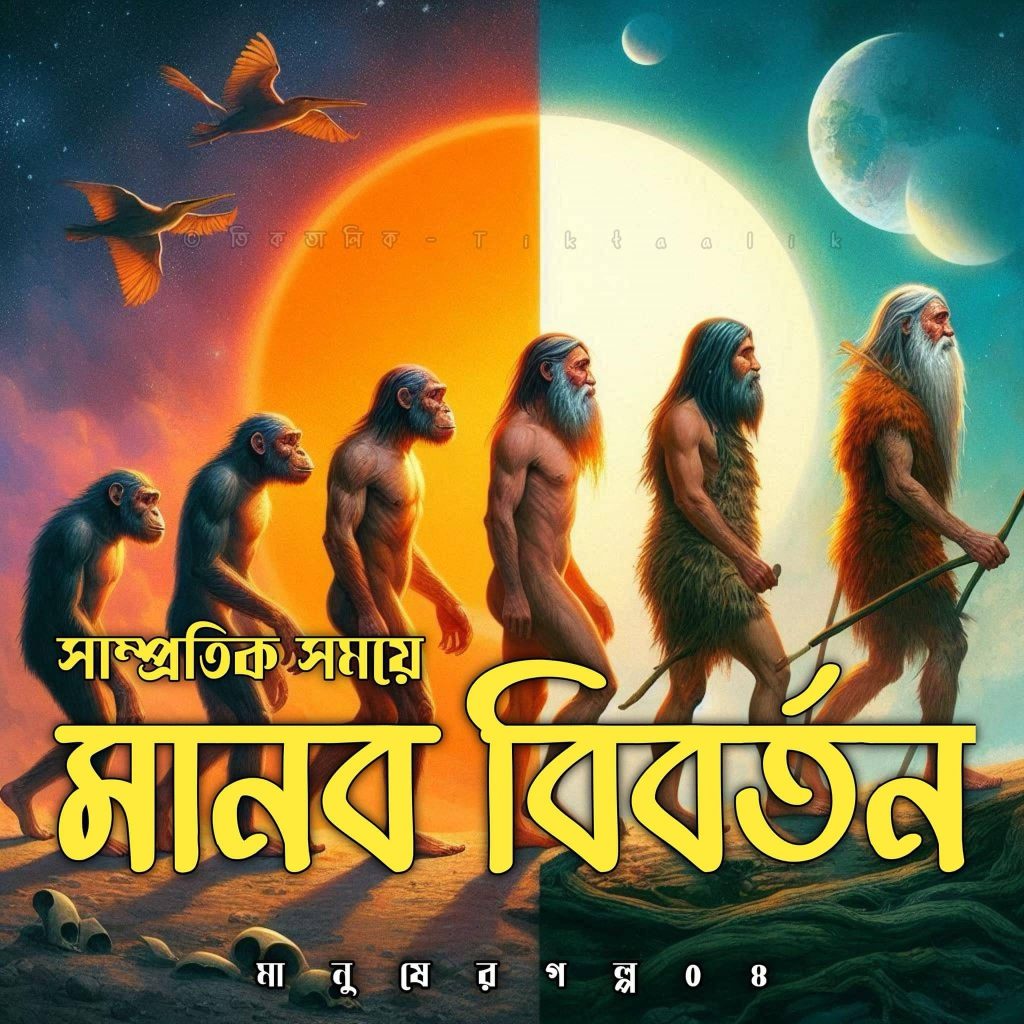
বিবর্তন নিয়ে আলাপের সময় প্রায়শই আমাদের দুটো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমত, বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রজাতির উৎপত্তি কি থেমে গেছে? এখন আর নতুন প্রজাতির উৎপত্তি কেনো ঘটছে না; দ্বিতীয়ত, মানুষের বিবর্তন বর্তমানে থেমে গেছে কিনা, মানুষের সাম্প্রতিক সময়ে কোনো বিবর্তনীয় নিদর্শন আছে কিনা এবং সবশেষে মানুষ বিবর্তিত হয়ে পরবর্তীতে কোন প্রজাতির আগমন ঘটবে পৃথিবীতে! শুরুতে আমাদের বুঝতে হবে বিবর্তন যেমন কয়েক ঘন্টায় হতে পারে তেমন কয়েক কোটি বছরও লাগতে পারে। নতুন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটতে কতসময় লাগবে সেটা নির্ভর করে আমরা কোন প্রাণীর বিবর্তন নিয়ে আলাপ করছি সেটার উপরে। ব্যাকটেরিয়ার নতুন প্রজাতি ২৪ ঘন্টা থেকে শুরু করে দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই তৈরী হতে পারে। নতুন প্রজাতি তৈরীর সবথেকে কম সময় এখন পর্যন্ত ২৪ ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই দ্রুতগতির বিবর্তনের পিছনে সবথেকে বড় কারণ- এদের ঘন ঘন প্রজনন ঘটা। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া ৪-৫ মিনিটেই নিজেদের সংখ্যা দ্বিগুণ করে ফেলতে পারে, গড়পড়তায় ২০ মিনিটের মধ্যেই কোনো স্থানে থাকা ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। এবার ভাবুন, কোনো স্থানে একটা মাত্র ব্যাকটেরিয়া থাকলে একদিন পর তার সংখ্যা কত হবে?
২০ মিনিট পরে হবে ১×২ = ২ টি।
৪০ মিনিট পর এই সংখ্যা হবে ১×২×২ = ৪ টি।
৬০ মিনিট তথা এক ঘন্টা পর ১×২×২×২ = ৮ টি।
২৪ ঘন্টা পর ঐ স্থানে তাদের মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ২^৭২ টি।
অর্থাৎ একদিনে মোট ৭২ বার পূর্ণ প্রজনন সম্পন্ন হবে এবং শেষ অবদি মোট ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা হবে ২^৭২টি। এবার হিসাব করুন তো, মানুষের ক্ষেত্রে এই ৭২ প্রজন্ম সম্পন্ন হতে কেমন সময় লাগতে পারে? যদি প্রতি ৩০ বছর পর পর কোনো পরিবারে একবার প্রজনন ঘটে এমন চিন্তা করি তবে এই ৭২ প্রজন্ম আসতে সময় লাগবে ৪০×৭২ = ২৮৮০ বছর প্রায়। আবার ২৮৮০ বছর পর কিন্তু ঐ মানব-পরিবারের সদস্যসংখ্যা মোটেও ২^৭২ এর মতো কোনো বড় সংখ্যা হবেনা। কারণ, মানুষ তার জীবনকালে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক বাচ্চাই উৎপাদন করে থাকে এবং ২-৩ প্রজন্ম পর পর পূর্ববর্তী প্রজন্মের সদস্যরা মারা যায় বয়সের কারণে। ফলে মানুষের সংখ্যা ব্যাকটেরিয়ার মতো সূচকীয় হারে বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব না কখনোই। প্রজননের সময়কাল এবং সদস্যসংখ্যার পরে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো “বিবর্তনের প্রক্রিয়া”। ব্যাকটেরিয়া যেহেতু ঘনঘন প্রজনন ঘটায়, তাই তাদের ডিএনএ প্রতিলিপি তৈরীর সময় ভুলত্রুটির পরিমাণও বেশি হয়ে থাকে। প্রতিলিপি তৈরীতে হওয়া এই ভুলত্রুটিকে পুঁথির ভাষায় বলে মিউটেশন। প্রকৃতকোষী প্রাণীদের শরীরে নানারকম ব্যবস্থা থাকে এই মিউটেশনকে সংশোধন করার জন্য। যত উন্নত জীব, যত জটিল জীব, তত তার মিউটেশন সংশোধন করার সক্ষমতাও বেশি। ফলে তর্কের খাতিরে সমান পরিমাণ মিউটেশন হচ্ছে ধরে নিলেও মানুষের মতো উন্নত জটিল জীবে তা অনেকাংশে সংশোধিত হয়ে যায়, যেটা ব্যাকটেরিয়ায় হয়না। ফলে নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে ব্যাকটেরিয়ায় যতবেশি প্রকরণ সৃষ্টি হয় আমাদের মধ্যে তত প্রকরণ হয়না।
ব্যাক্টেরিয়ার মতো আদিকোষীদের মধ্যে হরাইজন্টাল জিন ট্রান্সফার নামক একধরনের কৌশল দেখা যায় যার মাধ্যমে জেনেটিক তথ্য এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে তারা আদান-প্রদান করতে সক্ষম। অর্থাৎ আমাদের ক্ষেত্রে যেমন শুধুমাত্র পিতা-মাতা হতে সন্তানে জিন প্রবাহিত হতে পারে, ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে এক সদস্যের শরীর থেকে সরাসরি জিন অন্য সদস্যে যেতে পারে। ফলে উন্নত জীবের ক্ষেত্রে যেখানে নতুন কোনো মিউটেশন বা প্রকরণ গোষ্ঠীর সব সদস্যে ছড়াতে কয়েক কোটি বছর লাগে, ব্যাক্টেরিয়াতে এটা ছড়াতে লাগে কয়েকদিন! এবং নতুন মিউটেশনগুলো একবার পুরো গোষ্ঠীতে ছড়িয়ে গেলে ওই গোষ্ঠী নতুন প্রজাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এতসব সুবিধার ফলে ব্যাক্টেরিয়া কিংবা অন্য কোনো আদিকোষী জীবে জেনেটিক পরিবর্তন আসা, নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হওয়া যত সহজ এবং দ্রুততর, মানুষসহ যেকোনো জটিল জীবে সেটা এত দ্রুত গতির নয়। হাজার হাজার বছর লাগে কোনো একটা বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হতে, কোটি বছর লেগে যায় সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির আগমণ ঘটতে। প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছরের বিবর্তনে উদ্ভব হয়েছে বর্তমান প্রাণীকূলের। ২০২১ সালের হিসেব অনুযায়ী এখন পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি ১৩ লক্ষ প্রাণী প্রজাতি’র খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। এখনও প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রজাতি আবিষ্কৃত হচ্ছে। প্রতিটি প্রজাতিই এসেছে বিবর্তনের মাধ্যমে এবং বর্তমানে সেসকল প্রাণীদের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিবর্তন ঘটে চলছে। এই প্রবন্ধের মুখ্য আলোচনাই বর্তমান সময়ে মানুষের মধ্যে হওয়া বিবর্তনীয় নিদর্শনগুলো!
এখন পর্যন্ত ‘হোমো’ গণের ১৪ টি প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো কয়েকটি প্রজাতি খুঁজে পাওয়ার ভালোই সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এতগুলো প্রজাতির মধ্যে বর্তমানে টিকে রয়েছে মাত্র ১ টি প্রজাতি। হ্যাঁ, আর সেটি হলো ‘হোমো সেপিয়েন্স’। আমরা আমাদের আশেপাশে যত মানুষ দেখতে পাই; পৃথিবীর প্রায় ৮০০ কোটি মানুষ; সবাই এই হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতির অন্তর্গত। তবে এখন থেকে মাত্র কয়েকশ হাজার বছর পেছনে গেলেও মানুষের আরো কয়েকটি প্রজাতি খুঁজে পাওয়া যেতো। যেমন:
হোমো ইরেক্টাস: এরা এশিয়ায় ইতিহাসের দীর্ঘ একটা সময় কাটিয়েছে এবং স্যাপিয়েন্সদের সাথেও এদের সাক্ষাৎ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।
হোমো নিয়ান্ডারথালেন্সিস: এদের আমরা সবাই চিনি। ইউরোপ এবং এশিয়ার কিছু অংশে এদের বাস ছিলো। স্যাপিয়েন্সদের সাথে এরা অনেক বছর কাটিয়েছে, এমনকি যৌনমিলনের মাধ্যমে সন্তানও উৎপাদন করেছে। পরে বিভিন্ন প্রতিকূল কারণে নিয়ান্ডারথালরা বিলুপ্ত হয়ে যায়, এই প্রতিকূল কারণগুলির একটা ছিলো আমাদের পূর্বপুরষরা।
হোমো ডেনিসোভা: ডেনিসোভানরা নিয়ান্ডারথালদের নিকটাত্মীয় ছিলো। এদের বসবাস ছিলো এশিয়াতে। এদের সাথে স্যাপিয়েন্সদের প্রজননের প্রমাণ রয়েছে।
হোমো নালেডি: সাম্প্রতিক গবেষণায় পাওয়া তথ্যানুসারে হোমো নালেডি আড়াই থেকে তিনলাখ বছর পূর্বে আফ্রিকায় বসবাস করতো। এই সময়টাই স্যাপিয়েন্সদের পৃথিবীতে আগমনের সময়। অর্থাৎ নালেডি এবং স্যাপিয়েন্স একই সাথে ধরিত্রীতে অবস্থান করেছে একসময়।
হোমো রোডেসিয়েন্সিস: প্রাচীন মানবের এই প্রজাতি এক লাখ পঁচিশ হাজার বছর পূর্বেও পৃথিবীতে টিকে ছিলো। এই সময়কালের মধ্যে স্যাপিয়েন্স আফ্রিকা থেকে বের হয়ে দুনিয়া আবিষ্কার শুরু করেছিলো এবং ধারণা করা হয় নিয়ান্ডারথালদের মতো রোডেসিয়েন্সিসদের সাথেও স্যাপিয়েন্সদের প্রজনন-প্রতিযোগিতা দুটাই ঘটেছে।
জলবায়ুর পরিবর্তন, খাদ্য আশ্রয় নিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতা, অজাচারজনিত জেনেটিক ডিপ্রেশন আমাদের সাথী প্রজাতিদের বিলুপ্তির পথ প্রশস্ত করেছে। আজকের দিনে ভাবতে বসলে সবার মনে হতে পারে হোমো সেপিয়েন্স’ এ এসে মানুষের বিবর্তন থেমে গিয়েছে, নাহলে মানুষের আরও প্রজাতি থাকতো, এখন আর নতুন প্রজাতির উদ্ভব সম্ভব নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও সত্য নয়। বিবর্তন নদীর মতো প্রবাহমান একটি প্রক্রিয়া। প্রতিটি প্রাণী প্রজাতির মধ্যেই প্রতিনিয়ত বিবর্তন ঘটে চলছে। মানুষও তার ব্যতিক্রম নয় কোনোভাবেই। প্রবন্ধের বাকী অংশে আমরা বিভিন্ন কিস্তিতে আধুনিক মানুষ কিংবা হোমো সেপিয়েন্সদের মধ্যে ঘটা এবং ঘটতে থাকা সাম্প্রতিক কিছু বিবর্তন সম্পর্কে জানবো।
প্রথম কিস্তি: মস্তিষ্কের আকার পরিবর্তন
মানুষের বিবর্তনের ধারায় প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে মানুষের মস্তিষ্কে। সেই প্রাচীন এইপ’দের থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত মানুষের মস্তিষ্কের আকার ধীরে ধীরে বেড়েছে। হোমো গণের প্রথম দিকের প্রজাতি হোমো হাবিলিস’দের মস্তিষ্কের আকৃতি ছিল মাত্র ৬০০ ঘন সেন্টিমিটার। পরবর্তীতে সেই পরিমাণ বেড়ে গিয়ে হোমো নিয়ান্ডারথাল’দের মস্তিষ্কের আকৃতি হয়েছে ১৬৮০ ঘন সেন্টিমিটার। ব্যাপক পরিবর্তন!
তবে যদি হোমো সেপিয়েন্স দের কথা উঠে, তাহলে সমীকরণটা কিন্তু একটু অন্যরকম হয়। বিগত ৩০ হাজার বছরে হোমো সেপিয়েন্স’দের মস্তিষ্কের আকার ছোট হয়েছে প্রায় ১০ শতাংশ৷ এসময় মস্তিষ্কের আকার ১,৫০০ থেকে কমে ১,৩৫৯ ঘন সেন্টিমিটার হয়েছে৷ অর্থাৎ একটি টেনিস বলের সমান ঘনত্ব হ্রাস পেয়েছে৷ আর মস্তিষ্কের এই পরিবর্তন শুধু পুরুষদের ক্ষেত্রেই নয়৷ বরং নারীদের মস্তিষ্কেও ঘটেছে একই ধরণের পরিবর্তন৷ মস্তিষ্কের আকার ছোট হলেও তাতে মানুষ আরো নির্বোধ হয়েছে এমনটি নয়৷ বরং মানুষের বুদ্ধিমত্তা আরো প্রখর হয়েছে। মস্তিষ্কের আকার ছোটো হওয়ার বেশ কিছু হাইপোথিসিস রয়েছে। এর মধ্যে জনপ্রিয় একটি হাইপোথিসিস- ভাষার আবিষ্কার! ভাষার আবিষ্কার আমাদের তথ্য সংরক্ষণের সক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে। ফলে মস্তিষ্কের উপর তথ্যধারণ, বিশ্লেষণ এবং ব্যবহারের চাপ তুলনামূলক কমে আসছে। সোশ্যাল ব্রেন হাইপোথিসিস ব্যাখা করে কেনো সামাজিক জীব (বিশেষত প্রাইমেট) তুলনামূলক বড় মস্তিষ্কের অধিকারী হয়। যেকোনো সামাজিক জীবের দৈনন্দিন জীবনযাপনে চারটি অনিবার্য নিয়ামক রয়েছে। প্রথমত, প্রত্যেককে আলাদা আলাদা পরিচয়ে শনাক্ত করতে পারা। দ্বিতীয়ত, তাদের আচার-ব্যবহার দেখে তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারা। তৃতীয়ত, বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং চতুর্থত, যুদ্ধ এড়িয়ে মিলেমিশে টিকে থাকা। এসব সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য কগনিটিভ অ্যাবিলিটি অনেক বেশি হতে হয় যার দরুণ মস্তিষ্কের আকার সময়ের বিবর্তনে বৃদ্ধি পায়। প্রযুক্তির আবির্ভাব, ভাষার আবিষ্কার, নানারকম সরঞ্জাম তৈরী, নির্দিষ্ট স্থানে গোষ্ঠী গড়ে তুলে বসবাসের ফলে সামাজিক জীবনযাপন তুলনামূলক সহজ হয়ে আসে যার দরুণ বিগত কয়েক হাজার বছরে আমাদের মস্তিষ্কের আকারে বেশ কিছুটা হ্রাস দেখা গেছে। এছাড়াও আরোও কিছু হাইপোথিসিস রয়েছে যা নিয়ে পরবর্তীতে কখনো আলোচনা করা যাবে।
দ্বিতীয় কিস্তি: গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি
মানুষের বিবর্তনের আরেকটা প্রভাব দেখা যায় মানুষের আয়ু বৃদ্ধিতে। কয়েক কোটি বছর আগে প্রাইমেটদের আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র কয়েক বছর। ধীরে ধীরে সেটি বেড়েছে। মানুষের পূর্বপুরুষ’রা যখন বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো, তখন বিভিন্ন ইনফেকশন এর কারণে তাদের মৃত্যুহার বেশি ছিল। মাত্র ২০ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে চষে বেড়ানো হোমো হাবিলিস’দের গড় আয়ু ছিল প্রায় ১৩ বছর। মানুষের বিবর্তনের ধারায় সেটি ধীরে ধীরে বেড়েছে। হোমো নিয়ান্ডারথাল প্রজাতির সদস্যদের বেশিরভাগই ৪০ বছর পার হওয়ার আগেই মারা যেতো। মাত্র ৫০০০ বছর আগেও মানুষের অর্থাৎ হোমো স্যাপিয়েন্সদের গড় আয়ু ছিল ৪০ বছর। বর্তমানে সেটি দ্বিগুণের তুলনায় অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে। কিছু অঞ্চলে সেটি প্রায় ১০০ বছর ছাড়িয়ে গিয়েছে!
১৮০০ সালের পর মানুষের গড় আয়ু প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। মূলত জলবায়ু’র পরিবর্তন, খাদ্যাভ্যাস এবং নানা মরণব্যাধি’র প্রতিষেধক আবিষ্কারই এই পরিবর্তনে বড় প্রভাব ফেলেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধির ফলেই মানব প্রজাতি পুরো পৃথিবী দখল করতে সক্ষম হয়েছে এবং মহাকাশেও বিচরণ করছে। এখানেই ‘যোগ্যতমের উদ্বর্তন’ কথাটা আসে।
তৃতীয় কিস্তি: অধিক উচ্চতায় অক্সিজেন স্বল্পতায় বেঁচে থাকার ক্ষমতা লাভ
বিবর্তনকে আমরা মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। ডাইভার্জেন্ট এবং কনভার্জেন্ট বিবর্তন। সাধারণত একটা প্রজাতি অনেকগুলো গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। সময়ের সাথে সাথে কোনো প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে ভিন্ন ভিন্ন মিউটেশন দেখা যায়। আবার এই গোষ্ঠীগুলো ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে খাপ খাওয়াতে সেই পরিবেশ অনুযায়ী নিজেদের মানিয়ে নেয়, অভিযোজিত হয়। এভাবে গোষ্ঠী এবং প্রজাতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটে। এটাকে বলে “ডাইভার্জেন্ট বিবর্তন”, যেখানে সম্পূর্ণ একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রজাতির সদস্যরা বিবর্তনের ফলে ভিন্ন ভিন্ন নতুন বৈশিষ্ট্য এমনকি অঙ্গ-প্রতঙ্গ লাভ করছে। অন্যদিকে, “কনভার্জেন্ট বিবর্তনে” সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতির সদস্যরা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত হয়ে একই রকম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিংবা একই রকম শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। এরকমই এক গল্প আমরা এখন শুনবো যেখানে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী এমনকি প্রজাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় অভিযোজিত হয়ে একই বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।
সাধারণ মানুষের পক্ষে সমুদ্রপৃষ্ট হতে অধিক উচ্চতায় বসবাস করা অনেকবেশি কষ্টকর। কারণ, অধিক উচ্চতায় অক্সিজেনের জোগান কমতে থাকে। এ ধরনের স্বল্প অক্সিজেনযুক্ত পরিবেশকে বলে ‘হাইপোক্সিক’ পরিবেশ৷ আসলে শুধু মানুষের ক্ষেত্রে না, যেকোনো প্রাণীর পক্ষেই অনেক বেশি উচ্চতায় বসবাস করা দুরূহ ব্যাপার। যেসব প্রাণী অনেক উচ্চতায় যাওয়া আসা করতে সক্ষম, সেসব প্রাণীর শরীরে উচ্চ ঘনমাত্রার লোহিত রক্তকণিকা এবং হিমোগ্লোবিন থাকে, সাথে এদের ফুসফুসের বায়ুধারণের ক্ষমতাও অনেক বেশি যা তাদের ঐ উচ্চতায় টিকতে সহায়তা করে। কিন্তু মানুষের কিছু গোষ্ঠী দেখা যায় যারা এরকম অতি উঁচু স্থানে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে। তিব্বত, আন্দিজ এবং ইথিওপীয় অঞ্চলের মানুষজন এরই জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ। মজার বিষয় হলো, শুধু যে এসব এলাকার মানুষ গিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করেছে এমন কিন্তু না। এরা সেখানে নিজেদের গবাদিপশু, মুরগী, এমনকি কুকুর বিড়ালও নিয়ে গেছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এসব অঞ্চলের পাহাড়ে তথা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৫০০-৩০০০ মিটার উপরে বসবাস করছে তারা। যেখানে পৃথিবীর অন্য অঞ্চলের মানুষদের এসব জায়গায় ঘুরতে গেলেই অসুবিধা হয়, সেখানে এরা স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করেছে। এর কারণ এদের জিনগত পরিবর্তন এবং বহু বছরের অভিযোজন। যেমন: তিব্বতের যে জনগোষ্ঠী উঁচু স্থানে বসবাস করে, তাদের তিনটা জিনে মিউটেশন লক্ষ্য করা যায়। EPAS1, EGLN1 এবং PPAR। এর মধ্যে EPAS1 তাদের হিমোগ্লোবিনের ঘনত্বে প্রভাব রাখে যেখানে EGLN1 লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। ফলে এদের টিকে থাকার ক্ষমতা বেড়ে যায়। ফলে এই অঞ্চলের মানুষের রক্ত সংবহন তন্ত্রে অক্সিজেন পরিবহনের পরিমাণ সাধারণ অঞ্চলের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। এই EPAS1 জিনের মিউটেশনটি তিব্বতীয়রা পেয়েছে ডেনিসোভানদের থেকে- যাদের কথা প্রবন্ধের শুরুতে আলাপ করেছিলাম। বলেছিলাম ডেনিসোভান এবং স্যাপিয়েন্সদের প্রজননের কথা।
আন্দিজ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীতে আবার আলাদা মিউটেশন লক্ষ্য করা যায়৷ এদের RYR2 জিন আমাদের থেকে আলাদা। এই আন্দিয়ানদের শরীরে থাকা হিমোগ্লোবিন আবার বেশি পরিমাণে অক্সিজেনের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ সমপরিমাণ হিমোগ্লোবিন আমাদের শরীরে যে পরিমাণ অক্সিজেন পরিবহন করে, আন্দিয়ানদের শরীরে তার থেকে অধিক পরিমাণ অক্সিজেন পরিবহন করতে পারে। এই বৈশিষ্ট্য কিন্তু তিব্বতীয়দের মধ্যে ছিল না। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জেনেটিক মিউটেশন, ভিন্ন ভিন্ন শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন, কিন্তু ফলাফল একটাই। হাইপোক্সিক পরিবেশে টিকে থাকা। এই যে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে অভিযোজনের মাধ্যমে একই বৈশিষ্ট্য লাভ করা, এটাকেই বলে কনভার্জেন্ট বিবর্তন। এখানে আরও এক ধরনের কনভার্জেন্ট বিবর্তন কিন্তু ঘটছে। আগেই উল্লেখ করেছিলাম উক্ত জনগোষ্ঠীগুলো শুধু নিজেরা পাহাড়ের উচ্চতায় গিয়ে বসবাস শুরু করেনি, সাথে করে নিজেদের গবাদি পশু এবং গৃহপালিত প্রাণীও নিয়ে গেছে। তারাও নিজেদের মতো ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে অভিযোজিত হয়ে ওই উচ্চতায়, অক্সিজেনহীন পরিবেশে টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের ভিতরেও কোনো না কোনো জেনেটিক মিউটেশন, কোনো না কোনো শারীরবৃত্তিয় পরিবর্তন খুঁজে পাওয়া যাবে এবং এই নিয়ে বড় বড় গবেষণাও হয়েছে। কিন্তু আজ আর সে আলোচনায় যাবো না। এই অতি উচ্চতায় নিজেদের মানিয়ে নেওয়া মানুষের পরিমাণ কিন্তু নেহাতই কম নয়। প্রায় ৮১.৬ মিলিয়ন মানুষ এসব অঞ্চলে বসবাস করে। তাদের এই অভিযোজনের ক্ষমতা’কে বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক নির্বাচন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিজ্ঞানীদের ধারণা ১০০০-৭০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী সময়কালে তিব্বতের অধিবাসীরা এই ক্ষমতা অর্জন করে (মিউটেশন ঘটে)।
চতুর্থ কিস্তি: দুগ্ধজাত খাবার হজমের ক্ষমতা লাভ
ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স হলো এমন এক অবস্থা যেখানে ক্ষুদ্রান্ত্রে ল্যাকটেজ এনজাইমের অভাব হয়, যে শর্করা ল্যাকটোজ হজম করতে সাহায্য করে। ল্যাকটোজ একটি ডাইস্যাকারাইড, যা ল্যাকটেজ নামক এনজাইমের মাধ্যমে ভেঙে গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজে রূপান্তরিত হয়। এ ল্যাকটেজ এনজাইমের অভাবেই ল্যাকটোজ ভাঙতে পারে না। ফলে অসহনশীলতা বা ইনটলারেন্স দেখা যায়। ফলে দুধ খেলেই পেটে ব্যথা ও পাতলা পায়খানা হতে পারে। এ ছাড়া বমি ভাব, পেট ফুলে থাকা, পেট ভার হওয়া, পেটে গ্যাস হওয়া ইত্যাদি দেখা দেয়।
বর্তমানে আমাদের আশেপাশের অনেক মানুষই বয়স্ক হলে দুগ্ধজাত খাবার হজমে ব্যর্থ হয়। ফলে নানারকম পেটের রোগ দেখা দেয়। আবার, অনেকে দিব্যি সেসব খাবার হজম করতে পারে। এই ভিন্নতার কারণও লুকিয়ে আছে বিবর্তনের মাঝে। আমেরিকার প্রায় ১০ শতাংশ অধিবাসী, আফ্রিকার ১০ শতাংশ এবং চীনের প্রায় ৯৯ শতাংশ অধিবাসীই দুগ্ধজাত খাবার হজম করতে পারে না। তবে বাকি লোকেরা ঠিকই সেসব খাবার হজম করে ফেলে। মূলত মিউটেশনের কারণে ল্যাকটেজ এনজাইম এর ধারক জিনের পরিবর্তনে এমনটি ঘটেছে। প্রাচীন ইউরোপীয়’দের থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে দুগ্ধজাত খাদ্য হজমের ক্ষমতা আমাদের মাঝে এসেছে বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা। মানুষের অন্যান্য পূর্বপুরুষ কিংবা কাজিন প্রজাতি’দের মাঝে দুগ্ধজাত খাবার হজমে অক্ষমতা লক্ষ করা যায়। তাই এটিও মানুষের শরীরে সাম্প্রতিক বিবর্তনের একটি অন্যতম উদাহরণ।
পঞ্চম কিস্তি: হাতের পেশীতে নতুন ধমনীর উদ্ভব
মানুষের বিবর্তনের সবচেয়ে সাম্প্রতিক এবং উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হলো মানুষের হাতের পেশীতে নতুন ধমনীর উদ্ভব। অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড ইউনিভার্সিটি এবং ফ্লিন্ডার্স ইউনিভার্সিটির গবেষকরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, মানুষের হাতের সামনের অংশে অর্থাৎ ফোরআর্মের মাঝখানে একটি নতুন ধমনী (Artery) তৈরি হচ্ছে। ১৮৮০ এর দশকে, এই নতুন ধমনী-সহ বিশ্বে মানুষের সংখ্যা ছিল ১০ শতাংশ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণকারীদের ৩০ শতাংশের মধ্যে এই ধমনীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।
বিজ্ঞানীরা নতুন আবিষ্কৃত ধমনীটির নাম দিয়েছেন মিডিয়ান আর্টারি।
প্রাথমিকভাবে এই ধমনীটির জন্ম হয় যখন শিশু ভ্রূণে থাকে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এটি অদৃশ্য হয়ে যেত। এখন এই ধমনী বিলুপ্ত হচ্ছে না। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন রক্ত প্রবাহের জন্য শরীরের আরও একটি ধমনী প্রয়োজন। তবে এই ধমনীটি মানুষের শরীরে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে না বলে নিশ্চিত করেছেন বিজ্ঞানীরা। তবে ভবিষ্যতে এই ধমনীর বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে!
ষষ্ঠ কিস্তি: জলপরী ও মৎসকন্যার আগমন
তিমির বিবর্তন নিয়ে এক ছোটো তথ্য পড়ে অনেকেই মন্তব্য করেছিলেন, “স্তন্যপায়ী যদি বিবর্তিত হয়ে সবচেয়ে বড় সামুদ্রিক প্রাণী তিমি হতে পারে, তবে মানুষ কবে বিবর্তিত হয়ে জলপরী হবে?” তাদের সবার কাছে আমার প্রশ্ন ছিলো কী কী বৈশিষ্ট্য থাকলে কোন মানুষকে জলপরী হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে। আমার এই প্রশ্নের উত্তর যদিও বা কেউ দেননি, তবুও আমি ধরে নিচ্ছি জলপরী যেহেতু পানিতেই থাকে তাই তার পানিতে থাকার সক্ষমতা অনেক বেশি হতে হবে। এক ধরনের মানবগোষ্ঠীর পানিতে থাকার সক্ষমতা সাধারণ মানুষের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। এদেরকে বলা হয় বাজউ জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীর প্লীহার আকার সাধারণ জনগোষ্ঠীর তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি বড়। এই প্লীহায় লোহিত রক্তকণিকা জমা থাকে যা অক্সিজেন বহন করে থাকে। আমরা যখন পানির নিচে দীর্ঘক্ষণ থাকার চেষ্টা করি, তখন এই প্লিহায় থাকা লোহিত রক্ত কণিকার অক্সিজেন আমাদের জীবিত রাখে। বাজউ জনগোষ্ঠীর প্লিহা যেহেতু সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বড় তাই এদের প্লিহায় থাকা অক্সিজেনযুক্ত লোহিত রক্ত কণিকার পরিমাণও অনেক বেশি যা এদের দীর্ঘক্ষন পানির নিচে থাকতে সহায়তা করে। বাজউদের শরীরে PDE10A নামক একটি জিন থাকে যা তাদের এই প্লীহার আকার বৃদ্ধির পিছনে ভূমিকা রাখে। বাজউরা যখন সাঁতার কাটে তখন নিন্মোক্ত প্রক্রিয়ায় তাদের হৃৎস্পন্দন অনেক বেশি ধীরগতির হয়ে যায়। ফলে অক্সিজেনের ব্যবহারও হ্রাস পায়। প্লীহায় থাকা অতিরিক্ত অক্সিজেন এবং অক্সিজেনের কম ব্যবহার এই দুইয়ের কারণে তারা ১৩ মিনিট পর্যন্ত পানির প্রায় ২০০ ফুট নিচে থাকতে পারে। জেনেটিক আইসোলেশন এভাবেই থাকলে এই বাজউদের আসলেই আর কয়েক প্রজন্ম পরে জলমানব বা জলপরী আখ্যা দেওয়াই যাবে।
এছাড়াও ত্বকের উজ্জ্বলতা এবং চোখের রঙের পরিবর্তন, নিম্ন রক্তচাপ, শরীরে কোলেস্টেরল এর পরিমাণ পরিবর্তন, আলঝেইমার রোগের প্রাদুর্ভাব, ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি, মেয়েদের বিভিন্ন শারীরিক অবস্থার (menarche and menopause) পরিবর্তন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাইক্রো বিবর্তন এর প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। মাত্র এই কয় হাজার বছরে এত এত বিবর্তনীয় নিদর্শন থাকার পরেও মানুষ হতে পরবর্তী প্রজাতি সৃষ্টি এখনও অনেক দূর ভবিষ্যতের চিন্তা। ভেবে দেখুন, সব পরিবর্তন কিন্তু একই গোষ্ঠীতে হচ্ছেনা। ভাবুন, এমন এক মানব গোষ্ঠী যারা অতি উচ্চ পাহাড়ে সাবলীলভাবে বাঁচতে পারে, আবার পানির নিচে ২০০ ফুট গভীরতায় ১০-১২ মিনিট থেকে শিকার করতে পারে, যাদের চোখের রঙ, ত্বকের উজ্জ্বলতা আমাদের থেকে আলাদা, যারা দুধ হজম করতে পারেনা যেখানে আমরা পারি, যাদের হাতে নতুন ধমনী আছে যেটা আমাদের নেই ইত্যাদি ইত্যাদি, এমনটা যদি হতো তবে ওই গোষ্ঠীর মানুষ আমাদের থেকে অনেকখানিই আলাদা হতো। পরবর্তীতে আরও নতুন নতুন পরিবর্তন অভিযোজিত হয়ে সেই গোষ্ঠী আমাদের থেকে আরও বেশি আলাদা হয়ে যেতো এবং একসময় হয়তে আমরা তাদের আলাদা প্রজাতি হিসেবেই চিহ্নিত করতাম। কিন্তু তা হচ্ছেনা কারণ এত এত পরিবর্তন কালেরধারায় ঘটতে থাকলেও তা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে হচ্ছে, কোনো একটা গোষ্ঠীতে না। তাই নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটলেও সব মানুষ এখনও মানুষই আছে। এই বাজউরা ইদানীংকালে পানি ছেড়ে ডাঙায় ফিরে আসার প্রবণতা দেখাচ্ছে সুন্দর জীবনযাপনের জন্য। এর ফলে জেনেটিক আইসোলেশন একপ্রকার অসম্ভব বিষয় হয়ে উঠছে। জেনেটিক আইসোলেশন না ঘটলে এক গোষ্ঠীর সাথে অন্য গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য আদানপ্রদান চলতেই থাকবে এবং কোনো গোষ্ঠীতে এতটা পরিবর্তন কখনোই আসবেনা যে তাকে অন্য গোষ্ঠী থেকে আলাদাভাবে শনাক্ত করে প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করবো। এজন্য মানববিবর্তন মন্থর গতিতে আগাচ্ছে, কিন্তু থেমে যায় নি! আজকের আলোচনা এই পর্যন্ত, কোনো প্রশ্ন থাকলে মন্তব্যে জানাবেন। তিকতালিকের অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও পড়ে দেখার আহ্বান রইলো। ধন্যবাদ।
~ তিকতালিক-Tiktaalik